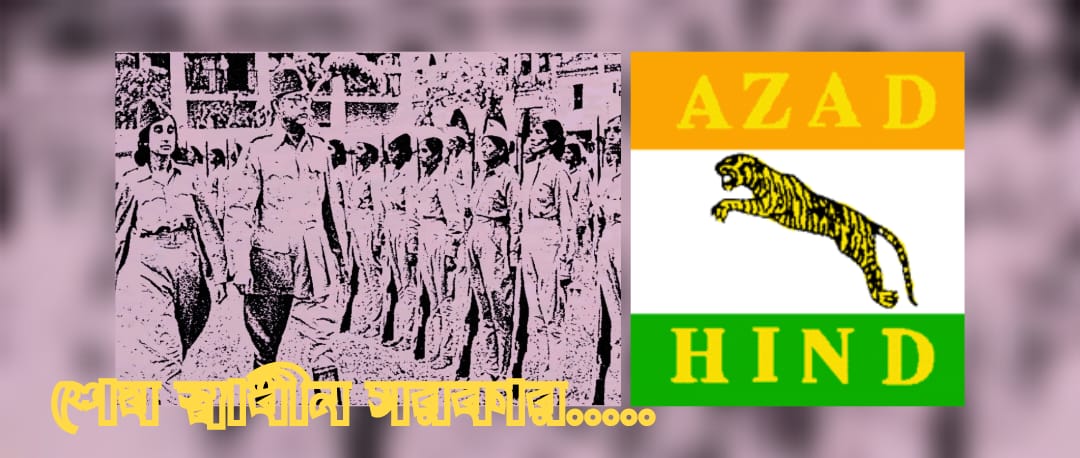২১ অক্টোবর, আজাদ হিন্দ দিবস।
By Bonhihotri Hazra
আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম ঘোষণায় সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ের পূর্বসূরি হিসেবে তুলে ধরলেন হাইদার আলি, সিরাজুদ্দউল্লা, টিপু সুলতান, বাংলার মোহন লাল, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কথা। এর আগে রেঙ্গুনে থাকাকালীন তিনি ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ-র মাজারে চাদর চড়িয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই সিপাহী বিদ্রোহের ধারাকে অনুসরণ করে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মের মানুষের একজোট হয়ে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা ধারাবাহিকতা আছে। সুভাষ বসু এবং তার আজাদ হিন্দ বাহিনী সেই ধারারই উত্তরাধিকার বহন করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২১ অক্টোবর ১৯৪৩-এ গড়ে ওঠে আজাদ হিন্দ সরকার। সুভাষ বসু এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। এস এ আইয়ার, কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি, লেফট কর্নেল এজাজ আহমেদ, লেফট কর্নেল এন এস ভগত, লেফট কর্নেল গুলজার সিং, লেফট কর্নেল এম জেড কিয়ানী, লেফট কর্নেল এ ডি লোগানাধান, লেফট কর্নেল ইশান কাদীর, লেফট কর্নেল শাহ নাওয়াজ খান, এ এম সাহায় এবং ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথান ছিলেন এই স্বাধীন সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীমন্ডলীতে। ২২ ও ২৩ অক্টোবর পরপর দুদিন অস্থায়ী সরকারের সভা বসে। সেখানে ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব পাশ হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জাপান, বর্মা, ক্রোয়েশিয়া, ফিলিপিন, নানকিং, মাঞ্চুকুও, শ্যাম ইতালী এবং জার্মানির মতো বিদেশী শক্তি স্বীকৃতি দিল এই বিকল্প সরকারকে। গোটা পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রবল আলোড়ন ফেলে এই প্রচেষ্টা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পুরুষ এবং মহিলারা এগিয়ে আসে বাহিনীতে যোগ দিতে অথবা অর্থ সাহায্য সহ নানা ভাবে সাহায্য করতে। ১৯৪৪ সালের ৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা করা হয় আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক। সুভাষ বসু ভাবেননি কেবল বিদেশের মাটিতে গঠিত এই বাহিনী একাই যুদ্ধে হারিয়ে ব্রিটিশকে ভারত থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হবে। তবে তাঁর আশা ছিল একবার মূল ভুখন্ডে আঘাত হানতে পারলে জেগে উঠবে দেশবাসী। ব্যপক জনগণ রাস্তায় নেমে পড়বে শেষ যুদ্ধের অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু বর্মা ফ্রন্টে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রবেশ করে তখন সেই আওয়াজ মানুষের কানে এসে পৌঁছয়নি। ভারতে সংবাদ মাধ্যমের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞার ফলে সুভাষ বসু ও আই এন এ-র সমস্ত খবর চাপা পড়ে যায়। আজাদ হিন্দ রেডিওর নিজস্ব সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ষে সব শোনা ছিল বে-আইনি আর সারা ভারতে মাত্র ১২,০০০০ বেতার যন্ত্র ছিল যা কেবল থাকা সম্ভব ছিল হাতে গোনা সচ্ছল পরিবারগুলির কাছে। তাই তখন যুদ্ধের খবর পৌঁছল না। তবে হ্যাঁ, সেই বাঁধভাঙ্গা জন জোয়ার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের সময়। ৪৬-এর উত্তাল সেই দিন গুলি ভারতকে সত্যিই হয়ত পৌঁছে দিয়েছিল বিপ্লবের দোরগোড়ায়। তবে সে সুযোগও বেরিয়ে গেল হাতের বাইরে। এ নিয়ে আলোচনায় ঢুকব যথাসময়। তবে এখন আলোচনা করব আজাদ হিন্দের বিকল্পের ভাবনা গুলো নিয়ে।
এই বিকল্পের ধারনার আর বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের চরম আঘাত দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা এই প্রথমবার দেখলাম, তা কিন্তু নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও একই ধরণের প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। দেখেছি স্বাধীন সরকার গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশের বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা।
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫। সেই দিনটা ফিরে আসবে না আর কোনও দিন। একশো বছরের বেশী পার হয়ে গেছে, সেভাবে কিন্তু কেউ মনে রাখেনি। সেই কোন দূর দেশ রাশিয়া থেকে এক বিপ্লবী ডাক পাঠিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সুযোগ নেওয়ার। লুঠেরাদের যুদ্ধকে স্বাধীনতার গৃহযুদ্ধে পরিণত করবার!
ডাক কানে পৌঁছেছিল গদরের। গদর পার্টির ডাকে দলে দলে দেশে ফিরছিলেন বিপ্লবীরা। দেশের মধ্যে মহাবিপ্লবের পরিকল্পনায় মেতে রয়েছেন তখন রাসবিহারী বসু। ওসব বোমা-গুলি-বন্দুক শুধু নয়, চাই উর্দিধারী কৃষকদের সমর্থন। ওঁরাও তো আমাদের দেশেরই লোক। ওদেরকে করতে হবে এককাট্টা। কোনও ধর্মের বিধিনিষেধ রাখলে হবে না। এই দেশ যতটা হিন্দুর, ততটা মুসলমানের, ততটাই শিখ ভাইদের আর ততটাই আদিবাসীদের। প্রচার চালানোর চেষ্টা হয়েছিল সবার।
সেই সারা ভারতবর্ষ তোলপাড় করা লাহোর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হলেন সাতজন। সর্বমোট অন্তত ৪৬ জন বরণ করেন শাহাদত। ফাসির দড়িতে, ফায়ারিং স্কোয়াডে বা জেলে নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়ে! তাঁদের অন্যতম কর্তার সিং সারাভা, বিষ্ণু গনেশ পিংলে, হরনাম সিং, জগত সিং, প্রমুখ।
সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেলেও সিঙ্গাপুর বাঁচিয়ে রাখল সেই স্বপ্নকে। ১৫ ই ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলা ইংরেজ অফিসারদের আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহের সূচনা করলেন চিস্তি খান, সুবাদার দাউদ খান, আবদুল আলি। চারদিনের জন্য সফল ভাবে সেখানে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে পারেন বিদ্রোহীরা, নামিয়ে দেওয়া হয় ইউনিয়ন জ্যাক।তবে তাদের জয়লাভ সুসংহত হওয়ার আগেই বিপুল সংখ্যক জাপানি ও ইংরেজ সৈন্য নির্বিচার হত্যালীলা চালিয়ে সিঙ্গাপুর আবার দখল করে! বিরাট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল এই সেনা অভ্যত্থানের। পেশোয়ার থেকে বাংলা বিশাল তার ব্যপ্তি। তবু বিশ্বাসঘাতকতার বিষ অঙ্কুরেই বিনাশ করল এত বড় সম্ভাবনাকে।
কিন্তু রাসবিহারীকে ধরা গেল না। কিছুতেই না। দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে রেখে গেলেন প্রতিশ্রুতি, “পরের সুযোগটা ছাড়বো না কিছুতেই”। হ্যাঁ, পরের সুযোগটা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ। ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং-এর ঐতিহাসিক সম্মেলনে নিজের হাতে গড়ে তোলা সংগঠন, সেনাবাহিনী এক মহান দেশপ্রেমিক তুলে দিলেন আরেকজন মহান দেশপ্রেমিকের হাতে। নিজের স্থান, প্রভাব প্রতিপত্তি সমস্ত যোগ্য উত্তরসূরির হাতে ছেড়ে নিজে সব আলোর বাইরে থাকাটা অত সহজ কথা কি? তবে এই হল ইতিহাস। এর পর সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর নিজের মতো করে এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্বাধীনতার যুদ্ধ, গড়ে তুললেন স্বাধীন সরকার। সেই সিপাহী বিদ্রোহ, গদর আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে আজাদ হিন্দ যার স্লোগান ছিল “ইত্তেফাক-ইতমিদ-কুরবানী” অর্থাৎ একতা-ভরসা-ত্যাগ। আজাদ হিন্দের আক্ষরিক অর্থ হল “মুক্ত ভারত” — সংস্কৃত শব্দ স্বরাজের পরিবর্তে, সুভাষ বসু আজাদ শব্দ ব্যবহার করেন, যা একটি উর্দু শব্দ, যা জনসাধারণ আপন করে নিতে পারে। তিনি হিন্দুস্তানী ভাষায় লিখিয়েছিলেন জাতীয় সঙ্গীত যা হিন্দি এবং উর্দুর সংমিশ্রিত ভাষা-হিন্দি নয়। প্রতিটা ক্ষেত্রে তিনি বিরত থেকেছেন এমন কোনও প্রতীক, স্লোগান বা শব্দ ব্যবহার করতে যা “হিন্দু” চিহ্ন হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে। সেই সময় যখন অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তরের মতো বিপ্লবী সংগঠনেও গীতা হাতে হয় শপথ গ্রহণ, কালীমূর্তিকে সামনে রেখে বিপ্লবীরা দেশের জন্য আত্মবলিদানে ঝাঁপিয়ে পড়েন আর বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে মুসলমান এবং নিম্নবর্গের থেকে- বিপ্লবের মঞ্চে জায়গা হয় না তাঁদের- সেই সময় দাঁড়িয়ে সচেতনভাবে এই প্রতীক বর্জন ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যের। আজাদ হিন্দের যাত্রার ছোট-বড় সমস্ত পদক্ষেপের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাব সুভাষচন্দ্র বসুর সত্যিকারের সেক্যুলার বোধের প্রতিচ্ছবি। এমন একটা সময়ে তিনি ঐক্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত তৈরি করতে সক্ষম হলেন, যখন দেশের মধ্যে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি সাম্প্রদায়িক সমস্যা আর বিভাজনের আশঙ্কা নিয়ে টালমাটাল।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে আজাদ হিন্দ ফৌজ
মনে রাখা জরুরী যে, নেতাজীর আজাদ হিন্দের লড়াইয়ে বিশাল সংখ্যায় মুসলিমরা অংশগ্রহণ করেছিল। সুভাষ বসুর নিকটতম সহযোগীরা মুসলমান। ভারত থেকে নিষ্ক্রমণের সময় থেকেই সুভাষ বসুকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম। আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন পেশোয়ারে সুভাষ বসুকে গ্রহণ করেছিলেন মিয়ান আকবর শাহ, যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন (NWFP)। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে সাবমেরিন যাত্রায় তাঁর একমাত্র ভারতীয় সহচর ছিলেন দক্ষিণের হায়দ্রাবাদের আবিদ হাসান। তিনি সম্ভবত ইউরোপ এবং এশিয়া উভয় ক্ষেত্রেই সুভাষ বসুর সবচেয়ে কাছের সঙ্গী ছিলেন। আইএনএর প্রথম ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন মোহাম্মদ জামান কিয়ানি। আমরা ইম্ফলের কাছে মইরাং-এ ভারতীয় তেরঙ্গা উত্থাপনের কথা বলি – যেটি শওকত মালিক নামে একজন আইএনএ অফিসার করেছিলেন। সুভাষের যে শেষ যাত্রার কথা জানা যায় সেখানেও তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন হাবিবুর রহমান। আমরা সকলেই জানি যে লাল কেল্লায়, ব্রিটিশরা একজন হিন্দু, একজন মুসলিম এবং একজন শিখ – প্রেম সাহগাল, শাহ নওয়াজ খান এবং গুরবক্শ সিং ধিলোনের বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মস্ত বড় ভুল করেছিল। এই তিন ধর্মের মানুষ আই এন এর উদ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক ঐক্যকেই তুলে ধরে। লাল কেল্লার সেই বিচার দেশ জুড়ে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়ে তোলে ব্রিটিশ বিরোধী দাবানল।
আইএনএ-তে খুব ভালো খ্রিস্টান অফিসাররাও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সিরিল জন স্ট্র্যাসি, যিনি সিঙ্গাপুরে আইএনএ মেমোরিয়াল নির্মাণ করেছিলেন।সুভাষ বসুর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বোধ এবং রাজনৈতিক পরিসর থেকে ধর্মকে বাদ রেখে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলনের চেতনা গড়ে ওঠার পিছনে আরেক জনের প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী, যাঁর কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি সুভাষ বসুর পূর্বসুরী- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ফ্রন্টেও দেশবন্ধুর কাজ ছিল অসাধারণ। চিত্তরঞ্জন দাশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সুভাষ বসু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভয়কে দূর করতে তাঁদের সত্যিই কাছে টেনে নেওয়ার জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁরা স্বদেশীর পর্যায় থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলায় নতুন উদীয়মান পেশা, শিক্ষা ও পরিষেবা ক্ষেত্রগুলোতে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। এটি সংশোধন করার জন্য, চিত্তরঞ্জন দাস “ব্রিটিশদের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা অর্জিত ক্ষমতা এবং অবস্থানের ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগির জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তির প্রস্তাব করেছিলেন”-যা ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ নামে খ্যাত।
সুভাষ বসু যখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হন, তখন তিনি কর্পোরেশনে বর্ণহিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে বড় সংখ্যক মুসলমানকে নিয়োগ করেন। এর জন্য বর্ণহিন্দুরা তাঁর কঠোর সমালোচনা করে কিন্তু তিনি মুসলিম, খ্রিস্টান এবং নিপীড়িত শ্রেণীর সদস্যদের ন্যায্য দাবীর প্রশ্নে অটল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এই পদক্ষেপে রাজনৈতিক হিন্দুত্বের অন্যতম কারীগর বিনায়ক সাভারকার হতাশ হয়ে বলেছিলেন যে “বোস মহাত্মা গান্ধীর থেকে খুব বেশি আলাদা না, তবে তিনি মুসলমানদের তোষণ করতে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন।”
আজাদ হিন্দ বাহিনীর এমন অনেক গল্প আছে যা আমাদের বারে বারে মনে করিয়ে দেবে সুভাষ বসু এবং আই এন এ-র অসাম্প্রদায়িক চেতনার দৃঢ়তা। সিঙ্গাপুরের অভিজাত চেট্টিয়ার পরিবার তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিল তাঁদের মন্দিরে যেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর ওজন পরিমান সোনা দান করবে তারা। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কিন্তু সাথে তাঁর অফিসারদের নিয়ে যান যাঁদের মধ্যে তিন জন ছিলেন মুসলমান। নিমন্ত্রণ কর্তার দোনামনা ভাব দেখে সুভাষ বসু মনস্থির করেছিলেন মন্দিরে ঢুকবেন না, ফিরেই যাবেন। তিনি বলেন- “যত বড় পরিমাণই হোক না কেন এই অনুদানের কোনও মূল্য নেই তাঁর কাছে যদি ধর্মের কারণে তাঁর অফিসারদের অসম্মান করা হয়।” শেষ অবধি চেট্টিয়ার পরিবার ক্ষমা চায় এবং সকলকেই মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যায়। তিলক সহ তাঁদের বরণ করা হলে মুসলমান অফিসারদের কেউ কিন্তু বাধা দেয় নি। যদিও মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে তিলক মুছে ফেলে সুভাষ বলেন, “আমি যদি ধর্মকে এই উর্দির সঙ্গে স্থান দিই তাহলে আমাদের সেনাবাহিনীই ভেঙে পড়বে।” এই ধর্মনিরপেক্ষতার বোধের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ সরকার যেখানে সমস্ত ধর্মীয় চিহ্নকে সচেতন ভাবে বাদ রাখা হয় রাজনীতির আঙ্গিনা থেকে।
আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা যোগী আদিত্যনাথরা ইতিহাসকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে নানাভাবে। ১২০০ বছরের গোলামি বলে তারা ব্রিটিশ শাসনের আগের সুলতান আমল বা মুঘল আমলকেও বিদেশী শাসন বলে দাগিয়ে দিতে চাইছে। ঔপনিবেশিক শাসকরা যে ইতিহাস চর্চার ধারাকে সামনে এনেছে দিল্লির সুলতান আমল বা মুঘল আমলকে বিদেশী শাসন বলে দাগিয়ে বা সেই যুগকে মুসলিম যুগ বলে চিহ্নিত করে তার জোর বিরোধিতা করেছেন সুভাষ বসু তাঁর ইন্ডিয়ান পিল্গ্রিম বইতে। তিনি বলেছেন যুগের এই নামকরণ ভয়ংকর ভুল। তিনি তথ্য সহ দেখিয়েছেন মুঘল আমলে কমান্ড্যান্ট চিফ, জেনারেল এবং মন্ত্রীমন্ডলী সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন হিন্দুরাই। একে কোনভাবেই মুসলিম যুগ বলা যায় না। ঔপনিবেশিক নির্মাণের অঙ্গ এই যুগের পর্যায়ভাগ আদ্যন্ত ভুল অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি।
আপনাদের যদি জিজ্ঞাসা করি- ‘কে জয় হিন্দ স্লোগানকে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্লোগান হিসেবে ফিরিয়ে আনল?’ অনেকেই বলবেন আবিদ হাসানের কথা। যদিও এর পিছনে একটা গল্প আছে। আমরা সকলেই জানি জার্মানি থেকে জাপানে সাবমেরিনে নেতাজির সহযাত্রী হওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় নেতাজীর সঙ্গী ছিলেন আবিদ হাসান। তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সাথী। পরবর্তীতে হাসান একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন যা সুভাষের ভাগ্নে শিসির বোসের স্ত্রী কৃষ্ণা বোস রেকর্ড করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকার অন্যান্য আরও কিছু নিবন্ধের সঙ্গে “নেতাজি: সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন, রাজনীতি এবং সংগ্রাম” নামে একটি বইতে প্রকাশিত হয়েছে। হাসান তাকে বলেছিলেন যে জার্মানিতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদেরকে নেতাজি ভারতীয় সেনা গঠনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের অনেককে তাঁর সাথে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্য শিবিরে তাদের সৈন্যদের জন্য উপাসনার স্থান আলাদা করে রাখা ছিল। মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা বা গির্জা যেকোনো ধর্মীয় স্থানে তারা উপাসনার জন্য যেতে পারত।
কিন্তু একবার ঐক্যের চেতনা থেকেই কিছু সৈন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে আবিদ হাসানের কাছে যান। তারা চেয়েছিল সৈন্যরা আলাদা আলাদা ভাবে প্রার্থনা না করে যদি একসাথে প্রার্থনা করতে পারে। হাসান খুশি হলেন। সৈন্যরা তখন একসাথে বসে একটি প্রার্থনা রচনা করে। পরের বার নেতাজি ক্যাম্প পরিদর্শন করার সময় তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ প্রার্থনা পাঠ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরিদর্শন শেষে, তারা নেতাজির সামনে দাঁড়িয়ে গর্বের সাথে তাদের সাধারণ প্রার্থনা এক কণ্ঠে পাঠ করেন। নেতাজি সেই মুহূর্তে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। কিছুক্ষণ পর, আবিদ হাসানকে একান্তে নেতাজির সাথে দেখা করার জন্য ডাকলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন -“এটা কী শুরু করেছ?”
তিনি আবিদকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন যে ভারতীয়দের একত্রিত করার এই পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এটি অবশ্যই পরিহার করা উচিত। তাঁর মত ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় এবং তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্মের কোনও ভূমিকা থাকা উচিত নয়। জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মীয় পরিচয়কে জোড়া একেবারেই উচিৎ না। এ নিয়ে আরও অনেক কথা এবং আলোচনা জরুরি। সে প্রসঙ্গে আসব পরে। তবে নেতাজির সংশয়ের জায়গা ছিল অন্যখানে। তিনি আবিদকে বলেছিলেন: “আজকে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে, আপনি অন্য কারোর জন্য দরজা খুলে দিচ্ছেন। সে কিন্তু একই অনুভূতি ব্যবহার করে আগামীকাল বিভাজনের বীজ বপন করবে।”
নেতাজির বিশ্লেষণের সঠিকতার উপলব্ধি আবিদ হাসানকে সমস্ত ভারতীয়দের জন্য একটি অভিবাদন সম্পর্কে চিন্তা করতে উদবুদ্ধ করেছিল। তারই ফলাফল ‘জয় হিন্দ’ – যা আজও জনপ্রিয় অভিবাদন হিসাবে রয়ে গেছে।
নেতাজির ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল গান্ধীর থেকে একেবারেই আলাদা; “সর্ব ধর্ম, সম ভাব” (সকল ধর্মের ঐক্য) চিন্তাধারা যা দিয়ে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- তা থেকে সুভাষের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা আলাদা। ঠিক এই ব্যাখ্যাটিরই তিনি এত কঠোরভাবে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর কঠোর অবস্থান- ধর্মকে রাজনীতি এবং প্রশাসনিক আঙ্গিনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে। সুভাষের এই সেক্যুলারিজমের ওপর কোনওদিনই দাঁড়ায়নি আমাদের দেশ। এখন “সংখ্যাগরিষ্ঠদের” ( যদিও সংখ্যা গরিষ্ঠতার ধারণা দাঁড়িয়ে আছে “দলিত, আদিবাসী সহ সকলেই হিন্দু”-জাতীয় মিথ্যের ওপর) রাজ প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া চলছে তার কথা তো ছেড়েই দিন এমনকি নেহেরুর হাত ধরে যে ধর্মনিরপেক্ষতা আমরা দেখেছি সেখানেও থেকেছে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় চিহ্ন- নারকেল ফাটিয়ে প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন, সরকারী স্কুল-কলেজে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সংবিধানে থাকলেও তা কখনই “ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের” কানাগলি থেকে বেরোতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে সুভাষ বসুর সচেতন ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলন দৃষ্টান্তমূলক।
জাত পাতের বিভাজন প্রশ্নে আজাদ হিন্দ ফৌজ
আজাদ হিন্দ বাহিনীতে বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সেনারা ছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে সেনা নিয়োগ মূলত করা হয়েছিল যুদ্ধ বন্দীদের থেকে। ব্রিটিশ বাহিনীতে জাতের নামে রেজিমেন্ট ছিল। আই এন এ-তে সেই সব জাত ভিত্তিক নাম পাল্টে গান্ধী ব্রিগেড, সুভাষ ব্রিগেড ইত্যাদি নাম দেওয়া হল। তবে নাম পাল্টালেও সম্প্রদায়গত গোষ্ঠী তৈরি করে থাকার প্রবণতা সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি। ব্রিটিশরা সুচারুভাবে বিভেদকে কাজে লাগাত কারণ সেটা তাদের নীতির অঙ্গ; কিন্তু এটা ঘটনা যে একধরনের বিভেদ নীচের তলায়ও ছিল। সেটা আই এন এ -তেও দূর করা যায়নি। তবে সমস্ত জাতের এবং ধর্মের মানুষের একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা ছিল যা সেই সময় দাঁড়িয়ে যথেষ্ট দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। সুভাষ বসু মনে করেছিলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে দিয়েই জাত-পাতের সমস্যা মিটে যাবে; এই প্রশ্নে আলাদা করে গভীর মনোনিবেশ করা বা ব্রাহ্মণ্যবাদের সমস্যাকে আলাদা করে দূর করার কোনও পদক্ষেপের কথা বলেননি। তবে সমস্ত জাত-পাতের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান বাড়ানো, একসাথে খাওয়া, ভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ে ইত্যাদিকে উৎসাহ দেবার কথা ভেবেছিলেন বিভাজন মেটাতে।
নারীদের অংশগ্রহণ প্রশ্নে আই এন এ-র দৃষ্টান্ত-
সিঙ্গাপুর পৌঁছে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের সময় সুভাষ বসু লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী হওয়ার কথা বলেন। শুধু তাই নয় তিনি তাকে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য মহিলাদের একটি রেজিমেন্ট বানাতে বলেছিলেন। লক্ষ্মী স্বামীনাথন তখন সিঙ্গাপুরে সদ্য ডাক্তারি পড়া শেষ করেছেন। মাদ্রাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে লক্ষ্মী। তাঁর পিতা মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনজীবী এবং মাতা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সিঙ্গাপুরে ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি লক্ষ্মী যোগ দিয়েছিলেন ‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগে’। প্রাণশক্তিতে চঞ্চল, সাহসীকতায় উজ্জ্বল, দেশপ্রেমে ভরপুর লক্ষ্মী নেতাজীর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবার আগে নারী বাহিনী গড়ে তোলার দায়ভার তুলে নিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুও লক্ষ্মীর মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর ক্যাপ্টেনকে, লক্ষ্মীও খুঁজে পেলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরুকে। তিন দিনের মধ্যে লক্ষ্মী একটি ২০ জন তরুণীর ইউনিট তৈরি করে রাইফেল নিয়ে একটি সভায় সুভাষচন্দ্রকে ‘গার্ড অব অনার’দিলেন। মেয়েরা সাদা শাড়িকে ইউনিফর্ম করে পরেছিল সেদিন। গোটা ব্যাপারটা আইএনএ-র সকলের যে খুব ভাল লেগেছিল তা নয়। প্রথম দিকে নারী বাহিনীর ভাবনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ছিল জাপানিরা। এদের প্রশিক্ষণের জন্য অস্ত্র শস্ত্র জোগান দিতে অস্বীকার করেছিল তারা। ভেবেছিল অর্থের অপচয় করা হবে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের প্রধান আট্টাবর ইয়েলাপ্পা জাপানি আপত্তির বাধা টপকে, ঝাঁসির রাণী বাহিনীর জন্য ব্যারাক ও অস্ত্র শস্ত্র জোগাড় করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মালয়(মালেশিয়া) ও বর্মার(মায়ানমার) প্রায় হাজার খানেক তরুণী যোগ দিয়েছিল এই বাহিনীতে।
লক্ষী সাইগাল পরে বলেছিলেন, ঝাঁসি রাণী রেজিমেন্টের ধারণা সম্পূর্ণ সুভাষ চন্দ্র বসুর মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনি বিপ্লবী ইতিহাসের একজন মহান ছাত্র। জোয়ান অফ আর্ক তাঁর অন্যতম নায়ক। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ আরেকজন। সেই আশ্চর্যজনক যুবতী যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসিতে, কাল্পিতে, গোয়ালিয়রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অশ্বারোহী একজন সাধারণ পুরুষের পোশাকে যুদ্ধে নিহত হন। সেই ঝাঁসির রাণির নামেই গড়ে উঠল আই এন এর মহিলা ব্রিগেড। সুভাষ বসু বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতার যুদ্ধে মেয়েদের কেবল দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না। তাঁদের সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ব্রিটিশদের নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং একই সাথে পুরুষের হাতে মেয়েদের অধিনতা থেকে মুক্তির পথও প্রশস্ত হবে। এমন জায়গায় পৌছনো সম্ভব হবে যাতে মেয়েরা জোরের সাথে সমানাধিকারের দাবী করতে পারে এবং অর্জন করতে পারে। সুভাষের সঙ্গী আবিদ হাসান বলেছেন যে অনেক আগেই সাবমেরিন যাত্রার সময় সুভাষ এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।সমাবেশে সুভাষ বসু এই রেজিমেন্টের প্রতি তার আশার কথা দীর্ঘক্ষণ ধরে হিন্দুস্তানি ভাষায় বলছিলেন। যথারীতি বেশিরভাগ মহিলা দক্ষিণ ভারতীয় হওয়ায় তা বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু একজন পুরুষ সেনা স্বেচ্ছায় অনুবাদ করতে গেলে লক্ষ্মী আপত্তি জানান। নারীদের নিজ কন্ঠে নারীদের কথা বলা উচিত-বলেন লক্ষী -এবং নিজেই অনুবাদ করার দায়িত্ব নেন। সুভাষ বসু লক্ষীকে বলেছিলেন -“ভাববেন না যে আমি এই মহিলা রেজিমেন্টকে শুধু একটি শোপিস হিসাবে রাখতে চাই। আপনাদের প্রশিক্ষণের পর আমি আপনাদের বার্মায় পাঠাতে চাই। আপনাদের বার্মার জঙ্গলে যুদ্ধ করতে হবে। এবং সেখানে এটা সহজ হবে না, কারণ মিত্রবাহিনী শক্তি জোগাড় করছে, তাই আমি চাই যে এই বাহিনীর গুরুত্ব কত সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হন ।” লক্ষ্মী তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং দৃঢ়তার সাথেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।
কীভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠল ঝাঁসির রাণী রেজিমেন্ট তার গল্প বলি বরং। প্রথমে পনেরোজন ঘটনাস্থলে সাইন আপ করেন। বাকি পাঁচজনের ছোট বাচ্চা ছিল এবং যোগ দিতে পারেনি। যদিও জাপানি বেসামরিক ব্যক্তি আমি এইমাত্র একটি মর্মস্পর্শী ছবি তুলে ধরেছে যে অল্পবয়সী স্বেচ্ছাসেবকরা ফুট ড্রিলের বিরতিতে তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন, বাস্তবে কিন্তু সদ্য যারা মা হয়েছে যাঁরা তাঁদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়নি। অন্যান্য বিবাহিতা মহিলাদের অবশ্য স্বাগত জানানো হয়েছিল। কখনও কখনও এমনও হয় যে দম্পতি একসাথে তালিকাভুক্ত হচ্ছে। মহিলা ঝাঁসি রেজিমেন্টের রানীতে আর তার পার্টনার একটি নিয়মিত ইউনিটে। তাই ধীরে ধীরে নিয়োগের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হয়। এর পর একটি ফাঁকা মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।কুয়ালালামপুরে সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা দিতে আসবেন জেনে এক অষ্টাদশী কন্যা জানকী থেবার বক্তৃতা শোনার জন্যে সভায় সাইকেল চেপে পৌঁছেছিলেন। অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের আবেগ ভরা বক্তৃতা শুনে। সভার শেষে দেখেছিলেন, অসংখ্য লোক সুভাষচন্দ্র বসুকে অর্থ সাহায্য করছেন, মহিলারা তাদের শেষ সম্বল গায়ের গয়না পর্যন্ত খুলে দিচ্ছেন দেখে তিনিও নিজের হীরের কানের দুল ও গলার চেন খুলে নেতাজিকে দিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় সাংবাদিক ছবি তোলায় পরের দিন সংবাদপত্রে ছবি দেখে বাড়িতে জানাজানি হয়ে যায়। তামিল ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে জানকী থেবার সমস্যায় পড়েন। জানকী দেবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ্মী স্বামীনাথন এসে সমস্যার সমাধান করেন। এরপর জানকী তাঁর সৎ বোন পাপাতি আর কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে ‘ঝাঁসির রানি বাহিনী’তে যোগ দিয়েছিল। তারপর একে একে যোগ দিয়েছিলেন রেঙ্গুনের বিশ্বভারতী একাডেমীর শিক্ষিকা মনাবতী আর্য, উচ্চবিত্ত পরিবারের দুই কন্যা মায়া ও অরুণা গাঙ্গুলী, মালয়ের দুই কিশোরী শামিতা ও অঞ্জলি ভৌমিক, সত্যবতী প্রমুখ। এই দৃষ্টান্ত সেই সময়ের জন্য অনেকটা এগিয়ে থাকা ভাবনার প্রতিফলন কারণ সেই সময় গান্ধীবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে সশস্ত্র ধারা সমস্ত ক্ষেত্রেই মেয়েদের পিছনের সারিতে থাকা ভূমিকাকেই ন্যায্য বলে দেখা হত। এমনকি চট্টগ্রামের মেয়ে প্রীতিলতা যে অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, শহিদ হয়েছেন – সেই ভূমিকা অর্জন করতে তাঁকে অনেক লড়াই করতে হয় সংগঠনের মধ্যেও। মাস্টারদা সূর্য সেনের গ্রুপে প্রীতিলতারই সহকর্মী অনন্ত সিংহ যেমন বারে বারেই ব্যক্ত করেছিলেন, মেয়েদের নেওয়ার সমস্যা হল- ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানান সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে, “পুরুষের কাজ আর নারীর কাজ” সংজ্ঞার বাইরে এসে মেয়েদের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার এই দৃষ্টান্ত অনেক তাৎপর্য বহন করে।
সুভাষ বসু বা আই এন এ কী ফ্যাসিবাদের ক্রীড়নক?
ঘনশ্যাম দাস বিড়লা যাঁকে ঈশ্বরদত্ত পরামর্শদাতা মনে করতেন গান্ধী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে জে এম কেইন্সকে একটি চিঠিতে লেখেন- “তাঁদের ভারত সাপ্রুর কথানুযায়ী রাজা পঞ্চম জর্জের সভায় মর্যাদাপূর্ণ জায়গা পাওয়ার মতো সুবিধা ছাড়া আর বেশী কিছু চায় না।” অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই স্বশাসন। নেহেরু গান্ধী সহ সব কংগ্রেস নেতাই তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বশাসনের পক্ষে। সুভাষ বসু এক নাগাড়ে পূর্ণ স্বরাজের আওয়াজ তুলছেন। কংগ্রেসের মধ্যে বাড়ছে দ্বন্দ। ক্রমশ সুভাষ বসুর কাজ করার জায়গা সঙ্কুচিত হচ্ছে। শেষমেশ কীর্তি কিসান পার্টির ভগতরাম তলোয়ার, রাম কিসানদের সাহায্যে দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পা রাখেন সুভাষ। সেখান থেকেই স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ লড়বার অঙ্গীকার তাঁর। তিনি প্রথমে সোভিয়েতেই যেতে চেয়েছিলেন সাহায্য চাইতে। কিন্তু সোভিয়েত সরকার তাঁকে ভিসা দেয়নি। বার্লিন যাওয়া প্রসঙ্গে সুভাষ বলেছিলেন-“বার্লিন বা রোমে যাওয়ার ব্যাপারে আমি খুশি নই কারণ সেখানে আমার কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই।” সোভিয়েত সম্পর্কে উচ্চকিত প্রশংসা বারে বারেই শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে। ১৯৪১ এ সোভিয়েত ইউনিয়নকে “বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি” বলে প্রশংসা করেছিলেন। এক জাপানি কর্মকর্তাকে একবার বলেন- “সোভিয়েতই একমাত্র শক্তি যে ব্রিটিশকে প্রতিহত করতে পারে। আমার ভাগ্য ওদের সঙ্গে বিজড়িত।” জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করল তখন তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৩৬ সালে প্যারিসে সুভাষ একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সভায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদ রুখতে চিন যাতে শক্তিশালী হয় সেকথা বলেন, এবং চিন-ভারতের যৌথভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের পক্ষে বলেন। চিনে জাপ বিরোধী লড়াইয়ের সময় সুভাষ বসু ‘চিন মেডিক্যাল মিশন’ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উনি বারবার সোভিয়েতের থেকে শেখার কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজনৈতিক বা মতাদর্শের নিরিখে শুধুমাত্র বন্ধু শক্তি নির্বাচন করলেই হবে না, যাঁরা ভিন্ন মতাবলম্বী প্রয়োজনে তাঁদেরও সহায়তা নিতে হবে কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে দেওয়া যাবে না। জাপানের সাহায্য নেবার পাশাপাশি চুক্তি করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্যই লড়বে। সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দকে ব্যবহার করে দেশের স্বাধীনতার লড়াইকে জোরদার করার কথা সব সময় ভাবতেন তিনি। মনে করতেন, এই পরিস্থিতিকে কাজে না লাগিয়ে নিরপেক্ষ থাকা আত্মহত্যার সামিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন বার বারই এসেছে বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যখন সাম্রাজ্যবাদের ভরকেন্দ্র থাকে দুর্বল, দ্বন্দে জর্জরিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেমন ঘটে রাশিয়ার বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে চিন বিপ্লব। আর শুধু রাশিয়া বা চিনই নয়- কোরিয়া, ইন্দোচিন, ইন্দোনেশিয়া, চিলি সহ দেশে দেশে বড় বড় পরিবর্তন এসেছে যুদ্ধের মধ্যে। সেই প্রেক্ষিত থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে উপনিবেশের শিকল থেকে মুক্তির চেষ্টার মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না। আজ দেখা যাচ্ছে একদিকে মার্কিণ এবং তাদের লেজুড় পশ্চিমী অর্থনীতি ধুঁকছে কিন্তু আহত বাঘের মতো ওঁত পেতে আছে যুদ্ধ লাগানোর অন্য আর অন্যদিকে চিনের অর্থনীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন-চিন বাণিজ্য যুদ্ধ দিন দিন আরও প্রকট চেহারা নিচ্ছে। আমেরিকা চিনের ইলেক্ট্রনিক ভেহিকেল সহ একাধিক পণ্যে কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই পরিস্থিতি অচীরেই বিশ্বযুদ্ধের দিকে গড়াতে পারে যার সুযোগ কাজে লাগানোর কথা ভাবা বিশেষ প্রয়োজন সুভাষ বসুর মতোই। আন্তর্জাতিক দ্বন্দকে কাজে লাগানোর এই রণকৌশল প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী জাতির কাছে যুগে যুগেই শিক্ষণীয়। সুভাষ বসু মনে করতেন বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করলে, দেশের মানুষ মনোবল পেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামবে। সেই আপোষহীন লড়াই এনে দেবে প্রকৃত স্বাধীনতার হাতছানি। তিনি মনে করতেন একবার দেশের বিপ্লবী শক্তি ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্তি পেলে, জার্মানি বা জাপানের মতো শক্তিও যদি ভারতকে গ্রাস করতে চায়, তাদের ঠেকানো সম্ভব হবে। যদিও এই বিশ্বাস কতটা বাস্তব সম্মত সে বিষয় প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা, সেইমতো সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে আপোষহীন থেকে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজের পথ করে নেওয়ার জন্য তিনি উপমহাদেশের জনগণের মনে আজও অবিস্মরণীয়; কিন্তু অবশ্যই প্রশ্নাতীত নন। ধর্মঘটের সময় তাঁর শ্রমিক বিরোধী ভূমিকাকে অনেকেই কঠোর সমালোচনা করেছেন যা সঙ্গত। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে ‘প্ল্যানিং কমিশন’ গঠন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু কেন্দ্রিকতার দিকে অতি মাত্রায় জোর, ভাষার প্রশ্নে এক ভাষা-এক জাতীয়তা ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার খানিক প্রবণতা তাঁর ক্ষেত্রেও ছিল বলেই মনে হয় যা বহু জাতির এই দেশে কতটা বাস্তব সম্মত তা আরও গভীর অনুসন্ধান দাবী করে, বিশেষ করে আজ যখন বহুত্বের প্রশ্ন আমরা বারে বারেই তুলছি ‘এক জাতীয়তা’র বিপরীতে। বিশেষ ভাবে এক ভাষাকে গড়ে তোলার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন হিন্দুস্থানি এবং রোমান হরফে লেখার ব্যাপারে। ভাষার প্রশ্ন এদেশে আজও অমীমাংসিত। একদিকে চলছে হিন্দি চাপিয়ে দেবার ব্রাহ্মণ্যবাদী কৌশল আর অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষাভাষীর মানুষের প্রতিস্বর। বহু প্রশ্ন থাকলেও উজ্জ্বল এক বিকল্প হিসেবে রয়ে গেছে আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ যা একদিন গোটা উপমহাদেশকে একসাথে জাগিয়েছিল। আজ টুকরো হয়ে যাওয়া উপমহাদেশে বসে এক ডাকে জেগে ওঠার সেই সন্ধিক্ষণ আলাদা মাত্রা এনে দেয়।
আজাদ হিন্দের বিচারঃ এক অসমাপ্ত বিপ্লবের কিছু মুহূর্তঃ-
প্রায় এক লক্ষ মানুষ এসে সামিল হয়েছিলেন সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে। মধ্য কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। আকারে খুব একটা বড় নয়। তাতে একেবারে ঠাসাঠাসি ভিড়! হবে নাই বা কেন। দিনটা হল ‘আজাদ হিন্দ দিবস’। ৫ নভেম্বর ১৯৪৫।
আজাদ হিন্দ দিবস কোনও বাৎসরিক পূজা অর্চনা বা নিয়ম মাফিক দিবস পালনের জন্য একেবারেই নয়। ১৯৪৫ সালে এই দিনটা পালন করা হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির দাবিতে। সারা দেশে ঠিক একই দিনে নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দিনে। সমস্ত জমায়েতে একটাই দাবী- নিঃশর্ত বন্দী মুক্তি।
গোটা পার্ক জুড়েই তুমুল ভীড়, আবার ওদিকে বিশাল এক মঞ্চ বানানো হয়েছে। মঞ্চের ডায়াসের সামনে সাজানো রয়েছে সুভাষচন্দ্র বোসের বিরাট এক প্রতিকৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস যদিও সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা নিয়ে একেবারেই প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু এইদিনের অনুষ্ঠানে তার বহিঃপ্রকাশ যেন না থাকে তাই নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর নেতারা। তাই অনুষ্ঠান সফল করতে হাজির হয়েছেন গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ। সেন্ট্রাল প্রভিন্স থেকে এসেছেন পন্ডিত রামশংকর শুক্লা। সমাবেশের সূচনা হল বন্দেমাতরম গান গেয়ে। গান চলাকালীনই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন খোদ বাংলার তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। এরপর গাওয়া হল ‘জন-গণ-মন অধিনায়ক…’। মঞ্চে এলেন আই.এন.এ. রিলিফ ফান্ড কমিটির সম্পাদক শ্রী অমিয় বোস। সকলের কাছে তিনি আবেদন রাখলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির জন্য ১, উডবার্ন পার্কের ঠিকানায় সাহায্য পাঠানোর। এর মধ্যেই বেজে উঠল আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধসঙ্গীত।
সভার মুখ্য এবং একমাত্র বক্তা ছিলেন সৈয়দ নৌসের আলি। তিনি ছিলেন বাংলা কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক। আরও বিষদ পরিচয় বললে বলতে হয়, তিনি ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত। তার উপর তিনি আবার ১৯৩৭-৩৯ পর্যন্ত বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার স্পিকার।
তো সেই বিরাট জনসভায় তিনি রীতিমতো হুমকির সুরে ঘোষণা করেন, ‘Touch a hair of the head of a single member of the Azad Hind Fauj and you commit an act of sacrilege which India will never forgive or forget’.তবে শুধু হুমকি দিয়েছেন বলেই যে আজাদ হিন্দ দিবস-এ তাঁর ভাষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এমনটা নয়। ৭ নভেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকার পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাবো আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর শিক্ষা থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্ন কেমন করে আবির্ভূত হয়েছিল ভারতীয় রাজনীতির মূল আঙিনায়। সেই লড়াইয়ে শুধু সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতাই নয়, উঠে এসেছিল লিঙ্গ বৈষম্য এবং জাতিবৈষম্যের মতন বিষয়গুলির প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আর নভেম্বর ৪৫’-এর কলকাতার লক্ষ মানুষ সেই নতুন চেতনাকে কীভাবে বিপুল উৎসাহে আপন করে নিয়েছিলেন—
‘The Azad Hind Fauj have already paved the way for national unity and have practically killed the demon of communalism. Hindus, Moslems, Sikhs and persons professing other religions composed the Azad Hind Fauj. They never thought, felt, talked or acted in terms of sects or communities. They ate together in the same mess, fought together and died together banishing all prejudices of caste, creed or colour. The rank and file, the officers and the Commander- in-Chief Subhas Bose ate the same food and ate it together. The brave daughters of India formed the Rani of Jhanshi Brigade under Captian Lakshmi. Thus the valiant children of India of both sexes and of all creeds formed themselves into an Indian army of independence for the emancipation of India from bondage. We may remember in this connection the desire of the officers awaiting trial that they would not accept any assistance from any communal organisation’.
সৈয়দ নৌসের আলি সাহেবের গলায় সেদিন অন্য এক আওয়াজ। কে জানতো দু’বছর পরেই এই উপমহাদেশ টুকরো হয়ে যাবে- বাংলার বুক চিরে গজিয়ে উঠবে কাঁটাতার। উনি বলছেন, “আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের ভিতর কখনো হিন্দুস্তান-পাকিস্তান ভেদ দেখা যায়নি, আর ভারতবাসী যেসব মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ছিটেফোঁটা এখনও বেঁচে রয়েছে, তাঁদের চোখ খুলে দিতে পারে আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্ম নিয়ে যুদ্ধের দিন শেষ; কারো ধর্ম পরিচয়ের জন্য আর কেউ তাঁর টুঁটি টিপে ধরবে না। বিশ্বের কোথাও আজ সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র সেখানেই আছে যেখানে শাসক তার নিজের স্বার্থে একে জিইয়ে রাখছে। স্বাধীনতা এলেই ওসব দূর হয়ে যাবে, আজাদ হিন্দ ফৌজ সেটা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে।”
এই অভ্যুত্থানগুলোর কয়েকটা বৈশিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত মনে রাখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বেই এই প্রতিবাদের সূচনা। সেই সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট। কোলকাতার রাস্তায় রেল এবং ট্রাম কর্মচারী এবং শ্রমিক থেকে শুরু করে চটকল শ্রমিক, ভ্যান-রিক্সা চালক তাঁদের জাতীয় হাতিয়ার ইঁট-পাথর-সোডা ওয়াটার ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গি চেহারায়। একেবার ভয় কাটিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন মারতে অথবা মরতে। এই আজাদ-হিন্দের বিচার কংগ্রেস-লীগ-শিখ-খাকসার আর কমিউনিস্টদের লাল পতাকাকে এক টানে একসাথে রাস্তায় নামিয়েছিল ঠিকই; তবে রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা যথেষ্ট নেতিবাচক। লোক দেখানো ডায়লগবাজিই সার। তার বাইরে সক্রিয়তা প্রায় নেই বললেই চলে। উপরন্তু কংগ্রেস নেতারা তো আন্দোলনকে ধামাচাপাই দিতে চাইছিলেন। যখন দেখলেন তা আর সম্ভব নয়, তখন তাঁরা দৃশ্যতই বিরক্ত। তবু হাওয়া বুঝে তাঁরাও আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তির দাবী তুললেন। আই এন এ ডিফেন্স কমিটি গড়ে উঠল ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অবিসংবাদিত কংগ্রেস নেত্রী অরুণা আসফ আলীর নেতৃত্বে। এদিকে সহকর্মীদের জন্য লেখা নোটে নেহেরু লিখছেন-“আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মীদের সেনাবাহিনীতে পুণর্নিয়োগের কোনও প্রশ্ন আমাদের সামনে নেই।” মুসলিম লীগ নেতাদের অবস্থাও তথৈবচ। পাকিস্তান প্রস্তাবের কী হবে তাই নিয়ে তাঁরা তখন উদ্বেগে। এর মাঝে জন দরদী ইমেজ রাখতে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গণ আন্দোলনে জায়গা পেতে তাঁরা কিছুটা পথে নেমেছেন। হিন্দু মহাসভা বা শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতি নগণ্য। নভেম্বরে এক আধ দিন ছাত্রদের সাথে দেখা গেলেও ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় না। কমিউনিস্টদের অবস্থা তুলনায় ভালো, কিন্তু তাঁরাও পরিস্থিতি বোঝার বা নেতৃত্ব দেবার জায়গায় ছিলেন না। জনগণের পাশে ছিলেন বটে কিন্তু এত বড় সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর কথা ভাবা তখন তাঁদের কল্পনার বাইরে। আসলে জনগণ যেন অনেক দূর এগিয়ে গেছেন-নেতারাই তৈরি নয়। কেবল হাত কামড়াচ্ছেন সোমনাথ লাহিড়ীর মতো হাতে গোনা কয়েকজন যাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছিলেন। এদিকে ছাত্ররা এবং নিম্ন বর্গের খেটে খাওয়া মানুষ কাজ বন্ধ রেখে, রেললাইন অবরোধ করে, ইঁট-পাথর হাতে গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে প্রস্তুত।
সমগ্র উপমহাদেশকে এক ডাকে জাগিয়ে বিপ্লবের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার উপাদান যে ছিল সেদিনের আজাদ হিন্দের বিকল্পে উত্তাল ৪৬-এর সেই সন্ধিক্ষণ তা দেখিয়ে দিয়েছে। এত ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সার্থকতা হয়ত সেখানেই নিহিত।
তথ্যসূত্রঃ-
১। শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত., সুনীতি কুমার ঘোষ অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (কোলকাতাঃসেতু প্রকাশনী, ২০১৯), ৪২-৬৯
২। Peter Ward Fay, The Forgotten Army India’s Armed Struggle for Independence 1942-1945 (New Delhi: Rupa)
৩। Sumanta Banerjee, Two Tragic Heroes of India: Subhas Bose and Charu Mazumdar (Kolkata: Thikthikana, 2022)
৪। Vera Hildebrand, Women At War Subhas Chandra Bose and the Rani of Jhansi Regiment (Noida: Harpers Collins Publishers, India, 2016)
৫। সন্দীপন সেন, প্রসঙ্গ জাপানঃ সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ, অণুষ্টুপ শারদীয় ২০২৪
৬। অনন্ত সিংহ, অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (কোলকাতা, র্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ২০১৬)
৭। রক্তিম ঘোষ, ৪৬-এর কোলকাতাঃ এক ভুলে যাওয়া যুদ্ধের কাহিনী, চারুপাঠ, তৃতীয় বর্ষ (কোলকাতা, খড়ি, ২০২৪)
৮। সুভাষ রচনাবলী ১ থেকে ১১ খণ্ড, (কোলকাতাঃআনন্দ, ১৯৮০)
৯। Harish K Puri, Ghadar Movement,(New Delhi: National Book Trust, 2011)
১০। গৌর অধিকারী, ভাবমূর্তিতে সুভাষচন্দ্র (কোলকাতাঃ মুক্তিচিন্তা পাবলিকেশন , ১৯৯৬)
১১। সৌম্য বসু, সম্পাদিত, নেতাজী উপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ (কোলকাতাঃ ছোঁয়া প্রকাশনী, ২০২২)
১২। S.A. Ayer, Story of The INA (New Delhi: National Book Trust, 2002)
১৩। শোভনলাল দত্তগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, ফ্যাসিবাদ ও জার্মানি, কোরক পত্রিকা, ১২৫ তম জন্মবর্ষে সুভাষচন্দ্র বসু (কোলকাতাঃ২০২২)
১৪। Subhas Chandra Bose, The Indian Struggle (Kolkata: Netaji Research Bureau, 1964)